নন্দিনী লুইজা
দুর্নীতি হলো এমন একটি অসত্ আচরণ, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজস্ব লাভ বা সুবিধার জন্য দায়িত্ব বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এটি হতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক—তবে মূল উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লাভ অর্জন। দুর্নীতিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করলে দাঁড়ায়, "কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইন, নিয়মনীতি, নৈতিকতা বা সামাজিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করে, তখন তাকে দুর্নীতি বলা হয়। ঘুষ: কাউকে বেআইনিভাবে সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ বা উপহার গ্রহণ এটা দুর্নীতি।
ক্ষমতার অপব্যবহার: নিজের অবস্থান বা ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে সুযোগ নেওয়া দুর্নীতি। দুর্নীতিপূর্ণ দরপত্র প্রক্রিয়া: সরকারি বা বেসরকারি টেন্ডারে স্বজনপ্রীতি বা লেনদেনের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে চুক্তি আদায় করা দূর্নীতি। জালিয়াতি: মিথ্যা বা প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ বা সুবিধা অর্জন করা দূর্নীতি। আত্মসাৎ: দায়িত্বে থেকে জনগণের বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করা দূর্নীতি। ফলে দুর্নীতি হলো —ন্যায়বিচার, সততা ও নৈতিকতার পরিপন্থী কাজ, যা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং এর ফলে সমাজ, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে দুর্নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্যাজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি প্রশাসনিক, আর্থিক এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে এবং এর ফলস্বরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি লোকসানের সম্মুখীন হয়। দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, কর্মক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, যার প্রভাব শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, পুরো দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনে পড়ে।
দুর্নীতি বলতে সাধারণভাবে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক কার্যক্রমে অবৈধ লাভ অর্জন করার জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা আইন বা নৈতিকতার লঙ্ঘনকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন রূপে হতে পারে, যেমন: ঘুষ, উৎকোচ, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি অর্থের অপচয়, সিস্টেমেটিক দুর্নীতি ইত্যাদি। প্রশাসনিক অদক্ষতা: দুর্নীতির কারণে প্রশাসনিক কার্যক্রমে অদক্ষতা তৈরি হয়, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, সেবা প্রদানে অস্থিরতা এবং মানুষের বিশ্বাস ভেঙে যায়। অর্থনৈতিক ক্ষতি: দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় খরচ বেড়ে যায়, যার কারণে পাবলিক অর্থের অপচয় হয়। এর ফলে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়মতো এবং সঠিকভাবে হয় না, যা দেশের অর্থনীতি দুর্বল করে। বৈষম্য বৃদ্ধি: দুর্নীতি উচ্চতর স্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হলে, এটি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সৃষ্টি করে এবং সাধারণ জনগণের জন্য সেবা পাওয়ার সুযোগ কম।
ভঙ্গ অস্বচ্ছতা এবং অপ্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম: সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির একটি বড় কারণ হল স্বচ্ছতার অভাব এবং সঠিক নিয়মনীতি না থাকা। যেখানে কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না বা তাদের কাজের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত তদারকি থাকে, সেখানে দুর্নীতি হতে পারে। ঘুষ এবং উৎকোচ: একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে ঘুষ ও উৎকোচের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে বিপথগামী করে এবং জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কমপ্লেক্স ব্যুরোক্র্যাটিক সিস্টেম: সরকারি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অফিসিয়াল প্রক্রিয়া, নিয়ম, ও পদ্ধতির কারণে মানুষ দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের কাজ দ্রুত করতে উৎসাহিত হয়।
এসব প্রক্রিয়া অত্যধিক জটিল এবং কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় হয়, যা দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। নিরীক্ষণের অভাব: দুর্নীতির প্রতিরোধে নিরীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু অনেক সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানে সঠিক নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া নেই। এতে সরকারি খরচ এবং সম্পদ অপব্যবহার ঘটানোর সুযোগ তৈরি হয়। দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসান অর্থনৈতিক ক্ষতি: দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সময়মত বাস্তবায়ন হয় না বা ত্রুটিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। যেমন, অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঘুষ খাওয়া, অনিয়মিত বিতরণ, অথবা মানহীন সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে প্রকল্পগুলোর খরচ বেড়ে যায় এবং ফলস্বরূপ লোকসান হয়। দক্ষ কার্যকারিতা কমে যাওয়া: যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, তখন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠান যেখানে চিকিৎসকরা ঘুষ নিয়ে রোগী দেখেন, সেখানে রোগীদের সঠিক চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে এবং আয় কমে যেতে পারে। ব্র্যান্ড মূল্য এবং জনসাধারণের আস্থা কমে যাওয়া: দুর্নীতি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয়। যখন সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির জন্য পরিচিত হয়, তখন তা জনসাধারণের জন্য কম আস্থাভাজন হয়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠানটি লোকসান বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাব: দুর্নীতির কারণে সরকার বা প্রতিষ্ঠান সময়মত তাদের পরিশোধযোগ্য দায় বা ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এর ফলে দায় পরিশোধে বিলম্ব ঘটে, যা আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।উদাহরণ হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির কারণে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।
উদাহরণ স্বরূপ: বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক: ব্যাংকটির বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হয়েছে। এছাড়া ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসানের সম্মুখীন হওয়া: একটি বিশ্লেষণ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়: প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে দুর্নীতির কারণে বেশ কিছু প্রকল্প সময়মত শেষ হয়নি এবং এর ফলে প্রকল্পের খরচ বেড়েছে, যার ফলে সরকারের উপর বোঝা পড়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রমের মানদণ্ড তৈরি করা এবং পর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এতে দুর্নীতি কমে আসবে এবং জনগণের আস্থা ফিরে আসবে।
কর্মী প্রশিক্ষণ: সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে তারা তাদের দায়িত্ব এবং নৈতিকতার প্রতি অবিচল থাকে এবং দুর্নীতি এড়াতে পারে। ডিজিটালাইজেশন: সরকারি কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করলে দুর্নীতির সুযোগ কমে যাবে এবং কাজের স্বচ্ছতা বাড়বে। দুর্নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা, যা শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের পুরো অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে। দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন লোকসানের সম্মুখীন হয়, তখন তা দেশের জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থমকে যায়। এই সমস্যা সমাধানে শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সঠিক প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন।









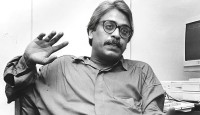
.jpg)
